
চলচ্চিত্রকে যদি আশ্চর্য এক আকাশ ধরা হয়, জহির রায়হান হলেন সেই আকাশের অন্যতম নক্ষত্র। যিনি ফাগুনকে দ্বিগুণ করার ফুলকি আঁকা শিখিয়ে জ্বলজ্বল করছেন আর্কটারাস তারার মতো। যিনি আদতে হতে চেয়েছিলেন চিত্রগ্রাহক কিন্তু পাকেচক্রে হয়ে গেলেন সাহিত্যিক, সাংবাদিক কিংবা রাজনৈতিক কর্মী। তবে তার চলচ্চিত্র নির্মাতা পরিচয়টিই সবচেয়ে রোশনাই ছড়িয়েছে।
চিত্রগ্রাহক হওয়ার নেশায় জহির প্রথমে কলকাতার প্রমথেশ বড়ুয়া মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট অব সিনেমাটোগ্রাফিতে ভর্তি হন এবং কিছুদিন পর সেই অধ্যায় শেষ না করেই ছেড়ে দেন। তবে হাতেকলমে তার চলচ্চিত্র শেখার পাঠ শুরু কিংবদন্তি নির্মাতা এ জে কারদারের কাছ থেকে। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘পদ্মানদীর মাঝি‘ অবলম্বনে নির্মিত ‘জাগো হুয়া সাভেরা’ (১৯৫৯) চলচ্চিত্রে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন তিনি। সালাউদ্দিন নির্মিত ‘যে নদী মরু পথে’তেও (১৯৬১) সহপরিচালকের ভূমিকায় থাকেন জহির। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রথমে অর্থনীতিতে, পরে বাংলা বিভাগে) থেকে পড়াশোনা শেষ করে নিজেই বানিয়ে ফেলেন সিনেমা।
তার প্রথম সিনেমা ‘কখনো আসেনি‘ (১৯৬১) বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম সেরা ও ব্যতিক্রমী এক সৃষ্টিকর্ম। ‘কাঁচের দেয়াল‘ তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ। তৎকালীন দুই পাকিস্তানের প্রথম রঙিন সিনেমা ‘সংগম’ (১৯৬৪) এবং প্রথম সিনেমাস্কোপ সিনেমা ‘বাহানা’ (১৯৬৫) নির্মাণ করেন জহির। ১৯৬৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘আনোয়ারা‘ ও ‘বেহুলা‘ জহিরের হাত দিয়ে মালা হয়ে বেরোয়। ‘জীবন থেকে নেয়া’ (১৯৭০) হলো এই চলচ্চিত্রকারের সবচেয়ে জনপ্রিয় সিনেমা। ‘লেট দেয়ার বি লাইট’কে নিজের স্বপ্নের সিনেমা বলতেন জহির রায়হান। ১৯৭০ সালে আংশিক দৃশ্যধারণ হলেও ছবিটি শেষ করে যেতে পারেননি। সর্বমোট ১১টি সিনেমা তার হাত দিয়ে রুপালি জগতে স্থান করে নেয়
জহির রায়হান ‘স্বাধীন বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের রূপরেখা’ কেমন হবে, তার পূর্ণাঙ্গ ধারণাপত্র তৈরি করেছিলেন। কিন্তু আমলাতন্ত্রের ফাইলের পাহাড়ে তা চাপা পড়ে যায়। আজও এ ব্যাপারে কাউকে উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায় না। জহিরের সহযোদ্ধা ও চলচ্চিত্র নির্মাতা আলমগীর কবির তার ‘ফিল্ম ইন বাংলাদেশ’ বইতে প্রথম জানিয়েছিলেন সেই ধারণাপত্রের কথা। সোভিয়েত বিপ্লবের পর ‘এজিট ট্রেন’ নামক এক প্রকার সিনেমা কারখানা গড়েছিল তৎকালীন রুশ সরকার, ঐ রকম চলচ্চিত্র কারখানার জাতীয়করণের কথা উল্লেখ ছিল তাতে। এছাড়া, জহির সিনেমার জন্য এমন সব উদ্যোগ নিতেন, যা তখন কারও ভাবনাতেই আসতো না। তিনি গঠন করেছিলেন ‘সিনে ওয়ার্কশপ’ এবং সেই ওয়ার্কশপ থেকে তার তত্ত্বাবধানে সিনেমা বানাতেন তরুণ নির্মাতারা।
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রামাণ্যচিত্র প্রযোজনা করেন জহির। এর ভেতর ‘স্টপ জেনোসাইড’ ও ‘আ স্টেট ইজ বর্ন’-এর নির্মাতা তিনি। স্টপ জেনোসাইডের মাধ্যমে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অকথ্য নির্যাতন, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের যাতনা, বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকারের দিনকাল ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছিল। উভয় সিনেমার মাধ্যমে বিশ্ববাসী কিছুটা হলেও একাত্তরের যুদ্ধের নৃশংসতার চিত্র দেখতে পায় এবং হানাদারদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে।
স্বাধীনতার পর ঢাকায় ফিরে জহির জানতে পারেন, ১৪ ডিসেম্বর থেকে নিখোঁজ রয়েছেন অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সার। বড় ভাইয়ের সন্ধানে ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি ঢাকার মিরপুরে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। জহিরের আর খোঁজ মেলেনি। স্বল্পায়ু জীবনে কত কী সৃষ্টি করে গেছেন কিন্তু স্বাধীন মাঠে সমতার বীজ বুনতে না পারার পরিতাপ ছিল তার? ‘লেট দেয়ার বি লাইট‘ শেষ করতে না পারার যন্ত্রণা? স্বপ্নদ্রষ্টা এই নির্মাতা ছিলেন বলেই হয়তো আলমগীর কবীর, বাদল খন্দকার বা তারেক মাসুদদের মতো নির্মাতার জন্ম হয়েছে এ দেশে। জহির রায়হান ছিলেন সেই লাইটহাউজের মতো, যিনি শুধু নিজের সময়কেই আলোকিত করেন না, পরবর্তী প্রজন্মের পথও প্রজ্বলিত করেন।
জহির রায়হান ‘আরেক ফাল্গুন’ নামে একটি বই লিখেছিলেন। বইটি ছিল বাংলা সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক প্রথম উপন্যাস। সেই বইয়ে বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কথা উঠে এসেছিল। সেখানে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের সংখ্যা দেখে ডেপুটি জেলার একপর্যায়ে বিরক্তি নিয়ে বলেছিল– ‘এত ছেলে জায়গা দেব কোথায়?’ জেলে থাকা একজনের প্রত্যুত্তর– ‘এতেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি? আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।’
চব্বিশের ছাত্র-জনতার আন্দোলন যখন উত্তাল, তখন শহরে শহর সেজেছিল গ্রাফিতির মোড়কে। দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাচ্ছিল মিছিলের গান, সূর্যস্লোগান। তার মধ্যে বুলেটের বিরুদ্ধে বুক উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল একটি রঙমশাল— ‘আসছে ফাগুন আমরা দ্বিগুণ হব’। সেই রঙমশাল থেকে ঠিকরে পড়ছিল গণমানুষের ক্রোধের আতপ। সেদিন শিক্ষার্থীদের তুলির আঁচড় হয়ে উঠছিল যেন পায়রার ডানা। সেই ডানা ঝাপটানোর কম্পাঙ্ক ছড়িয়ে যায় দেশ থেকে দেশে আর জহির উল্লাহ থেকে জহির ‘রায়হান’ হওয়ার গল্প লুটোপুটি খায় অনুচ্চারিত অক্ষরে..
















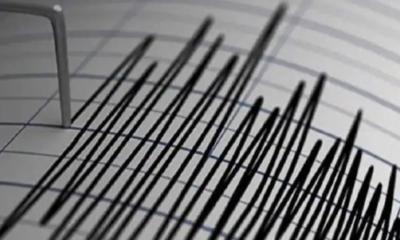















আপনার মতামত লিখুন :